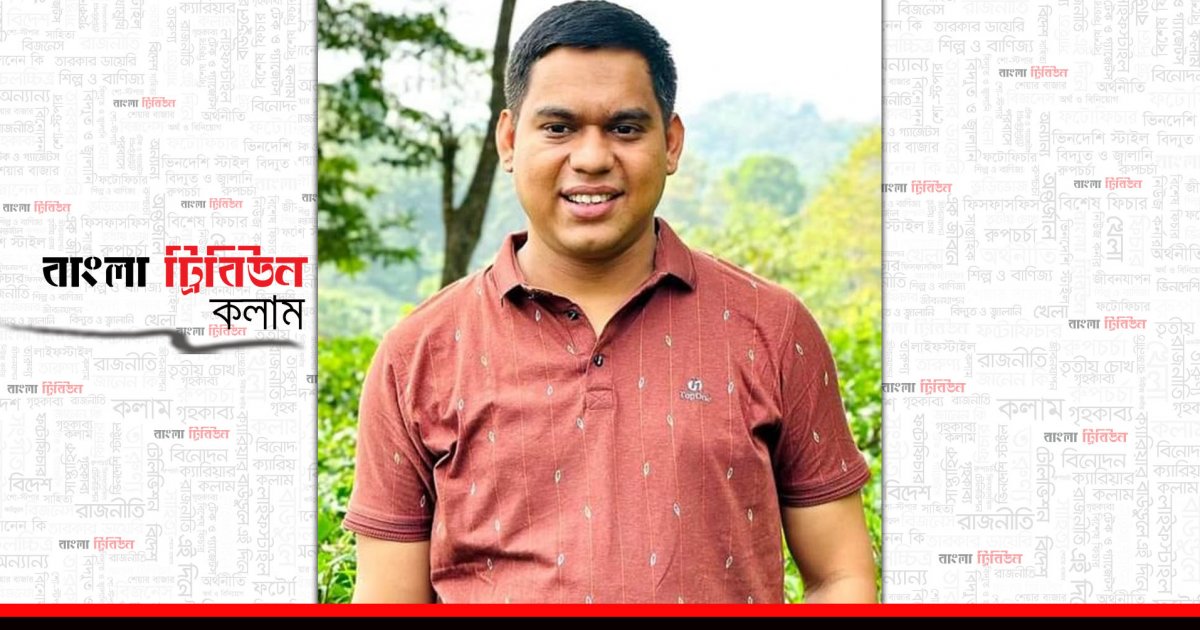আফগানিস্তান হলো এমন এক দেশ, যার নাম উচ্চারণ মানেই ইতিহাসের এক অগ্নিময় অধ্যায়ের কথা মনে পড়ে। পাহাড় ঘেরা কাবুল, কান্দাহার, হেরাত কিংবা মাজার-ই-শরিফ যেন একেকটি সাক্ষ্য বহন করছে বহু শতাব্দীর সংঘাত, রাজনীতি আর পরাশক্তির খেলা। এই ভূখণ্ডটিই ছিল তথাকথিত “গ্রেভইয়ার্ড অব এম্পায়ারস” যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন শুরু হয়েছিল। আমেরিকা তার ২০ বছরের যুদ্ধ শেষে ফিরে গিয়েছিল, আর এখন সেখানে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে আছে তালেবান। এই বাস্তবতায়, ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্ক নতুন করে আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—যে বয়ান আমরা ভারতীয় মূলধারার মিডিয়ায় দেখি, তা কি সত্যিই বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন, নাকি সেটি তৈরি হচ্ছে এক বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে?
বন্ধুত্বের ইতিহাস
স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ। ১৯৫০ সালে দু’দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় বন্ধুত্ব চুক্তি, যা পরবর্তীতে উন্নয়ন, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক সহযোগিতায় নতুন অধ্যায় খুলে দেয়। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় শিক্ষক, দিল্লিতে আফগান শিক্ষার্থীদের বৃত্তি। এই সম্পর্ক ছিল মানবিক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের প্রতীক। তবে, ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতি পাল্টে যায়। পাকিস্তান তখন মার্কিন ঘনিষ্ঠ হয়ে আফগান মুজাহিদিনদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। ভারত, তার বিপরীতে, সোভিয়েত ঘনিষ্ঠ অবস্থানে থেকে কাবুলে বৈধ সরকারকে সমর্থন করে। এই অবস্থান ভারতের কূটনীতিকে এক জটিল পথে ঠেলে দেয়। কারণ ইসলামাবাদের মাধ্যমে আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা জোট। তবু ভারত তার কূটনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রাখে। ২০০১ সালে তালেবান সরকারের পতনের পর, আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে ভারতের ভূমিকা হয়ে ওঠে উল্লেখযোগ্য। দিল্লি স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা, পার্লামেন্ট ভবন নির্মাণে অর্থায়ন করে। ভারতীয় সাহায্য প্রকল্পগুলো আফগান জনগণের কাছে সুনাম অর্জন করে। কিন্তু ২০২১ সালের আগস্টে, আমেরিকার সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবান দ্বিতীয়বার কাবুলে প্রবেশ করলে ভারতের সব হিসাব গুলিয়ে যায়। এই পরিবর্তনের পর থেকেই ভারতীয় মিডিয়ায় আফগানিস্তানকে ঘিরে শুরু হয় নতুন এক প্রচারণা।
মিডিয়ার বয়ান: ভয়, হুমকি ও “পাকিস্তানি ছায়া”
২০২১-এর পর ভারতীয় মূলধারার মিডিয়াগুলোর শিরোনামগুলো লক্ষ্য করলে একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা যায় “তালেবান মানেই পাকিস্তান”, “আফগানিস্তান হয়ে উঠছে ভারতের নিরাপত্তার হুমকি”, “কাশ্মিরের জঙ্গি হামলায় আফগান ছায়া”—এমন ধরনের সংবাদ ও বিশ্লেষণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন- টাইমস নাও, রিপাবলিক টিভি কিংবা জি নিউজের মতো টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রচার করতে থাকে যে, আফগানিস্তানের নতুন শাসকগোষ্ঠী ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ‘স্ট্র্যাটেজিক ডেপথ’ হিসেবে কাজ করছে। তালেবানকে তারা একমাত্রিকভাবে “সন্ত্রাসবাদী” হিসেবে তুলে ধরে, কিন্তু একইসঙ্গে কোনও কোনও চ্যানেল আবার ভারতীয় কূটনীতির সাফল্যের গল্পও বলে। যেন ভারত কাবুলের নতুন শাসকদের সঙ্গেও যোগাযোগে সক্ষম। এই দ্বৈত বয়ান আসলে ভারতীয় অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রতিফলন। বিজেপি সরকারের নেতৃত্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক বর্ণনা চায় জনগণের মধ্যে একপ্রকার নিরাপত্তা সচেতনতা বা ভয় তৈরি হোক। যাতে রাষ্ট্রীয় নীতির কেন্দ্রে “জাতীয়তাবাদ” আরও দৃঢ়ভাবে বসে। ফলে আফগানিস্তান নিয়ে সাংবাদিকতার বদলে প্রোপাগান্ডা-মুখী কভারেজই বেশি দেখা যায়।
বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার অনুপস্থিতি
ভারতের কিছু প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম যেমন দ্য হিন্দু, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বা স্ক্রল.ইন তুলনামূলকভাবে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার চেষ্টা করে। তারা দেখিয়েছে তালেবান শাসনের মধ্যেও ভারত কীভাবে তার অর্থনৈতিক ও মানবিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখছে, বিশেষ করে কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের সীমিত পুনরায় চালু হওয়ার বিষয়টি। কিন্তু টিআরপি-নির্ভর টেলিভিশন সাংবাদিকতা এই বিষয়গুলোকে আড়াল করে, এবং দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করে “গ্লোবাল হিন্দুত্ব” বনাম “ইসলামি চরমপন্থা”-র এক সরলীকৃত দ্বন্দ্ব। এই প্রেক্ষাপটে আফগান নাগরিকদের কণ্ঠ একেবারেই অনুপস্থিত। খুব কম সংবাদই পাওয়া যায় যেখানে কাবুল বা কান্দাহারের মানুষ সরাসরি তাদের মতামত দিতে পেরেছে। ভারতীয় টকশোতে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে নয়াদিল্লির নিরাপত্তা বিশ্লেষক, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, কিংবা সাংবাদিকদের উত্তপ্ত বিতর্ক। যেখানে বাস্তব তথ্যের চেয়ে উত্তেজনা ও আবেগই মুখ্য।
আফগানিস্তান ভারতের কাছে কী? বন্ধু না কৌশলগত পণ্য?
ভারতের জন্য আফগানিস্তান কখনও শুধু এক বন্ধু দেশ নয়; বরং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগ স্থাপনের এক ভূরাজনৈতিক দরজা। মধ্য এশিয়ার গ্যাস ও বাণিজ্যপথে প্রবেশের কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবেও আফগানিস্তানকে দেখা হয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ভারত সেখানে সামরিক বা রাজনৈতিক উপস্থিতি রাখতে পারছে না। চাবাহার বন্দর কিংবা ইরান-আফগান ট্রানজিট রুটে চীন ও পাকিস্তানের প্রভাব বাড়ছে। ফলে ভারতীয় মিডিয়ায় এই ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবকে আড়াল করতে গিয়ে “মনস্তাত্ত্বিক বিজয়” দেখানোর প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, “তালেবান ভারতের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী”, “ভারতের মানবিক সহায়তায় আফগান জনগণের আস্থা”—এই ধরনের প্রতিবেদন আসলে বাস্তবের তুলনায় অতিরঞ্জিত। অন্যদিকে, ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম দূরদর্শন বা সরকারি ন্যারেটিভে আফগানিস্তানকে “মানবিক সংকটের শিকার মুসলিম দেশ” হিসেবে তুলে ধরা হয়, কিন্তু সেখানে তালেবান শাসনের পরিবর্তে জোর দেওয়া হয় পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রে। এর ফলে, ভারতের জনমনে গড়ে ওঠে এক ধরনের একপাক্ষিক ধারণা যে আফগানিস্তান ভারতের শত্রুদের ঘাঁটি হয়ে উঠছে।
মিডিয়া-রাষ্ট্র সম্পর্কের দ্বন্দ্ব
ভারতের গণতন্ত্রে মিডিয়া একসময় ছিল শক্তিশালী চতুর্থ স্তম্ভ। কিন্তু বর্তমান সময়ে বহু গণমাধ্যম রাজনৈতিক ক্ষমতার ঘনিষ্ঠতায় বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। আফগানিস্তান ইস্যুতে এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট। সরকারি কূটনৈতিক নীতি অনুযায়ী কভারেজ তৈরি হচ্ছে, সমালোচনামূলক প্রতিবেদন খুব কমই দেখা যায়। যেমন—যখন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে, কাবুলে মানবিক সহায়তার মাধ্যমে তালেবান প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, তখন বেশিরভাগ চ্যানেল সেটিকে “কূটনৈতিক সাফল্য” বলে প্রচার করে। কিন্তু কেউ প্রশ্ন তোলে না যে সহায়তা কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে, কিংবা সেই সহায়তার বিনিময়ে ভারত কী ধরনের রাজনৈতিক ছাড় দিচ্ছে? এই অবস্থায় সাংবাদিকতা হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিধ্বনি। “নিউ ইন্ডিয়া”-র প্রোপাগান্ডায় আফগানিস্তানকে ব্যবহার করা হয় জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাত হিসেবে।
বিকল্প বয়ান: দক্ষিণ এশিয়ার সমন্বিত দৃষ্টিকোণ
সব সাংবাদিক একই সুরে কথা বলেন এটা কিন্তু ঠিক না। কিছু স্বাধীন গবেষক, সাংবাদিক ও ব্লগার চেষ্টা করেছেন বিকল্প বয়ান উপস্থাপন করতে। যেখানে আফগানিস্তানকে দেখা হয় দক্ষিণ এশিয়ার এক অভিন্ন মানবিক সংকটের অংশ হিসেবে, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নয়। তারা মনে করেন ভারতের উচিত আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ককে “মানবিক কূটনীতি”-র আলোকে দেখা, যেখানে নারী শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুনর্গঠনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় মিডিয়ায় খুব সীমিত জায়গা পেলেও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে।
আফগানদের চোখে ভারত : আশা না অবিশ্বাস?
যদিও তালেবান সরকার ভারতের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি, তবু কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের পুনরায় খোলার খবর আফগান জনগণের একাংশে আশার সঞ্চার করেছে। বিশেষ করে যারা অতীতে ভারতীয় শিক্ষাপ্রকল্পের সুবিধাভোগী ছিলেন, তারা চান ভারত আবার তাদের পাশে দাঁড়াক। কিন্তু একই সঙ্গে একটি বড় অংশ মনে করে ভারত তাদের ব্যবহার করেছে নিজের কৌশলগত স্বার্থে। কারণ তালেবানকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় ভারত নিষ্ক্রিয় ছিল। এমনকি তখনও দিল্লি কেবল পশ্চিমা জোটের দিকে তাকিয়ে ছিল। এই কারণে আফগানিস্তানে ভারতীয় প্রভাব আজ অনেক কমে গেছে। ভারতীয় মিডিয়া এই আত্মসমালোচনার জায়গাটি প্রায় এড়িয়ে যায়। তারা দেখাতে চায় ভারত “আফগান জনগণের প্রকৃত বন্ধু”, অথচ আফগান কণ্ঠকে কখনও শোনা হয় না।
বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠি
ভারতীয় মিডিয়ার আফগানিস্তান কভারেজকে যাচাই করতে গেলে তিনটি মাপকাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে—
১. তথ্যের উৎস : অধিকাংশ প্রতিবেদনের উৎস সরকারি ব্রিফিং বা আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা। স্থানীয় সূত্র বা স্বাধীন সাংবাদিকের তথ্য প্রায় অনুপস্থিত।
২. বর্ণনার ধরন : অধিকাংশ সংবাদেই “আমরা বনাম তারা” দৃষ্টিভঙ্গি—যেখানে আফগানিস্তানকে কেবল হুমকি হিসেবে দেখানো হয়।
৩. মানবিক দৃষ্টিকোণ : নারী শিক্ষা, খাদ্য সংকট, শরণার্থী সমস্যা—এসব ইস্যু অনেক কম গুরুত্ব পায়, যদিও এগুলোই বাস্তব আফগানিস্তানের মুখ্য সমস্যা।
এই তিনটি মানদণ্ডে বিচার করলে বোঝা যায় ভারতীয় মিডিয়ার বয়ান আংশিক সত্য, কিন্তু পুরো সত্য নয়।
ভবিষ্যৎ পথ: কূটনীতি ও সাংবাদিকতার ভারসাম্য
ভারত যদি সত্যিই আফগানিস্তানে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পুনরুদ্ধার করতে চায়, তবে কূটনীতি ও সাংবাদিকতার মধ্যে একটি নতুন ভারসাম্য দরকার। প্রথমত, আফগান জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের পথ বাড়াতে হবে—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবিক প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়িয়ে। দ্বিতীয়ত, মিডিয়ার উচিত আফগান বাস্তবতা নিয়ে “গ্রাউন্ড রিপোর্টিং” বাড়ানো, যাতে ভারতীয় জনগণও বুঝতে পারে আসল পরিস্থিতি কী।তৃতীয়ত, সাংবাদিকদের উচিত রাষ্ট্রীয় ন্যারেটিভ থেকে বেরিয়ে স্বাধীন বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা। কারণ কোনো দেশের প্রকৃত বন্ধু সে-ই, যে তার সত্য কথা শুনতে পারে, কেবল প্রশংসা নয়।
শেষকথা: বাস্তবের বাইরে বয়ানের দেয়াল
ভারত–আফগানিস্তান সম্পর্ক আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ভারত চায় তার প্রভাব ফিরিয়ে আনতে, তালেবান চায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে, আর আফগান জনগণ চায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা। এই তিনটি লক্ষ্য একে অপরের বিপরীত নয়, কিন্তু সঠিক ভারসাম্য ছাড়া সম্ভব নয়। ভারতীয় মিডিয়া যদি সত্যিই সেই বন্ধুত্বের ইতিহাসকে ধরে রাখতে চায়, তবে তার প্রথম দায়িত্ব সত্যকে বিকৃত না করা। কারণ সাংবাদিকতার কাজ হলো আলো জ্বালানো, কুয়াশা তৈরি করা নয়।আফগানিস্তান আজ শুধু একটি ভূখণ্ড নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার বিবেকের পরীক্ষা। ভারতীয় মিডিয়া যদি তার বয়ানকে আত্মসমালোচনার আয়নায় না দেখে, তবে সেই সম্পর্ক কাগজের পাতাতেই থেকে যাবে। বাস্তবের বন্ধুত্ব আর পুনর্গঠনের মাটিতে সম্ভব হবে না।
লেখক: গণমাধ্যম শিক্ষক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক

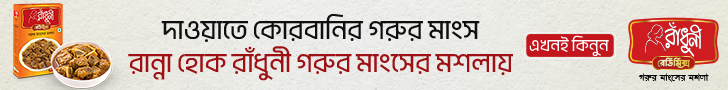
 Voice24 Admin
Voice24 Admin