এই যে অপ্রাপ্তিতে, অপূর্ণতায়, অসম্পূর্ণতাতেও এক অমলিন, অসূয়াহীন, অক্ষয় প্রেমের রূপ, তাতেও মিলেমিশে, জড়াজড়ি করে থাকে অভিমানের এক অনবদ্য রূপ। নজরুলের চোখ দিয়েই আমি দেখেছি, জেনেছি যে ‘চির-সুদূর প্রিয়তম’কে সর্বান্তঃকরণে চেয়েও ‘পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম’ আক্ষেপ না হয়ে, অনুযোগ না হয়ে বরং আরও বেশি করে ভালোবাসতে শেখায়। সেখানে ‘মূরতি ধরি তুমি নিরুপম’ ঠিক পাশে এসে না দাঁড়ালেও ‘নিখিলের রূপে রূপে, দেখা দাও চুপে চুপে’। সেই প্রেমকে ছিনিয়ে নেয় , সাধ্য কার! এমনকি সেই ‘তুমি আকাশের চাঁদ’ হলেও ‘আমি পাতিয়া সরসী-ফাঁদ’ অপেক্ষায় থাকি। আর অভিমানেই হয়তো প্রগাঢ় ভালোবাসা তার নীরব কিন্তু প্রবল উপস্থিতি ‘জনম জনম কাঁদি কুমুদীর সম’ বলে জানান দিয়ে যায়। এই কান্নাতে লজ্জা নেই, অনুশোচনা নেই বরং আছে দেদীপ্যমান ভালোবাসা আর অনির্বাণ বিরহ।
অভিমানী নজরুলের গানে গানেই অনুভাবে এল, এমনকি এই চিরবিরহী রূপে অসম্ভব জেনেও আমরা মিলনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ থাকি। আর এই প্রতীক্ষা আছে বলেই ‘সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি’ রহি’’ আর আছে অভিমানের সজল কান্না। শতসহস্র প্রচেষ্টায়ও ভালোবাসাকে ‘বুকে তায় মালা করি’ রাখিলে যায় সে চুরি, বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি’। কেননা ‘সে থাকে নীল নভে…সাতাশ তারার সতীন-সাথে সে যে ঘুরে মরে’ আর ভাসি ‘আমি নয়ন-জল-সায়রে’। সেই শৈশবে ‘চোখে মলিন কাজল লেখা, কণ্ঠে কাঁদে কুহু কেকা’ শব্দবন্ধে যেমন অভিমানের মূর্তরূপকে চিনে নিতে শিখেছিলাম, যার রূপ ছিল মলিন, ভাব ছিল ‘করুণ’। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৈশোরে যখন প্রেমের সঙ্গে জানাজানি হলো, তখন বুঝলাম অভিমানে কাজল লেখা মলিন হলেও, এতে কোনো মালিন্য নেই, নেই বঞ্চনাবোধ। অভিমানের ‘করুণ’ রসেও আছে ভালোবাসতে পারার অনন্য, অনবদ্য অনুভব। ‘কাজল করি’ যারে রাখি গো আঁখি-পাতে, স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপনে অশ্রু-সাথে’ শব্দবন্ধের গভীরতায় পরম প্রেম আর অভিমান একাকার হয়ে যায়, সেখানে বেদনা হয়ে ওঠে এক জীবন পরিক্রমার সঞ্জীবনী, সৃজনীশক্তি। তাই নজরুল লিখতে পারেন—
‘আমার অন্তর্যামী জানেন তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কী গভীর ক্ষত, কী অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমায় কোনোদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমানিক না দিলে আমি “অগ্নিবীণা” বাজাতে পারতাম না। আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না…যাক আজ চলেছি জীবনের অস্তমান দিনের শেষে রশ্মি ধরে ভাটার স্রোতে, তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর। আর তার চেষ্টা করো না।’
জোর করে ভালোবাসা আদায় না করে, সরে এসে, ছেড়ে দিয়েও যে আরও প্রবল করে ভালোবাসা যায়, তা–ও আমি জেনেছি নজরুলের গানে, তাঁর কবিতায়, লেখায়। আর এই নিঃশব্দ কিন্তু প্রগাঢ় ভালোবাসা নিঃস্বার্থ, চাহিদাহীন। অভিমানে যেমন নিবেদন আছে, অনুরাগ আছে, ঠিক তেমনি আছে আকাঙ্ক্ষাহীন নিরাসক্তি। কী অপূর্বময়তায় তাই অভিমানী নজরুল সুরের গাঁথুনিতে লিখতে পারেন—
‘আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে
আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশ, বেণী যাবে যবে খুলিতে।।
তোমার সুরের নেশায় যখন, ঝিমাবে আকাশ কাঁদিবে পবন
রোদন হইয়া আসিব তখন, তোমার বক্ষে দুলিতে।।’
অবহেলা পেলেই অবহেলা ফিরিয়ে দিতে হয় না আর অবহেলার অভিমান নিয়েও ভালোবেসে যেতে পারলে অনন্য ভিন্নমাত্রিক পূর্ণতা মেলে। তাই ‘অভিমানী গৃহহারা’ কবি লিখতে পারেন ‘জোর করে কেউ বাঁধে না তাই বুক ফুলিয়ে চলিস বিজয়রথে’।
নজরুলের জীবনকে, তাঁর মনন, মানস, বোধকে জানার প্রয়াসে, তাঁকে নিয়ে পড়তে গিয়ে বারবার অনুভব করেছি তাঁর জীবনে বারবার এসেছে দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, দুঃখ, মৃত্যুশোক। এত সব যন্ত্রণা কি তাঁকে আরও বেশি করে অভিমানী করে তুলেছিল? এই যে তাঁর কবিতায়, গানে, লেখায় অভিমানের ছায়া চোখে পড়ে, অভিমানকে ভর করে ধূমকেতু হয়ে ওঠবার স্পৃহা নজরে আসে, তা–ও কি সেই পোড় খাওয়া, নানান আঘাতে–অভিঘাতে জর্জরিত জীবনের দান?
‘রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, “দ্যাখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলির মতো, কিটসের মতো খুব বড় একটা ট্র্যাজেডি আছে, তুই প্রস্তুত হ”। জীবনে সেই ট্র্যাজেডি দেখার জন্য আমি কত দিন অকারণে অন্যের জীবনকে অশ্রুর বরষায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছি। কিন্তু আমারই জীবন রয়ে গেল বিশুষ্ক মরুভূমির মতো দগ্ধ। মেঘের ঊর্ধ্বে শূন্যের মতো কেবল হাসি, কেবল গান, কেবল বিদ্রোহ।’
অমন করে যেই কবি বলতে পারেন, তখন বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে কী সুতীব্র অভিমানের অনুভব থেকে তিনি গান বেঁধে বলেন, ‘কাঁটার ঘায়ে কুসুম করে ফোটাব মোর প্রাণ’। আর অমন কাঁটার ঘায়ে হৃদয়ে নিয়ত ক্ষরণ হতো বলেই তিনি প্রত্যয়ী হয়ে বলতে পারেন, ‘আঘাত যত হান্বে বীণায় উঠ্বে তত তান’। বারবার অভিমানী নজরুল বলেছেন চরম অসহায়তায়, পরম অপূর্ণতায় গানের মাঝে, গানের সঙ্গলাভে তিনি জিয়ন–কাঠির পরশ লাভ করেছেন, আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তাই তো তিনি বলেন, ‘ভুলতে তোমার অবহেলা, গান গেয়ে মোর কাট্বে বেলা’। গানে গানে তিনি কেঁদেছেন, আবার সেই অশ্রুজলে মনের আগুন নিভিয়ে সুন্দরকে, কল্যাণকে, প্রীতিকে, প্রেমকে খুঁজে গেছেন, মানুষের জয়গান গেয়ে গেছেন। নানান বন্ধকতা এসেছে, পাড়ি দিতে হয়েছে বন্ধুর পথ। অভিমান ছিল, কিন্তু অভিযোগ না করে, অনুযোগ না এনে ভালোবাসায় ভর করে জীবনকে উপভোগ করেছেন আর আমাদেরও শিখিয়ে গেছেন অপূর্ণতাতে, অপ্রাপ্তিতেও জীবন অর্থবহ হতে পারে, উদ্যাপিত হতে পারে।
কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি। কবি চায় প্রীতি। কবিতা আর দেবতা সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয়, যা সুন্দর তাই দিয়ে। সুন্দরের ধ্যান, তার স্তবগানই আমার ধর্ম। তবু বলছি, আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি।
‘বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে’ জন্মগ্রহণ করে কী অনবদ্য দৃঢ়তায় নজরুল বলতে পেরেছিলেন ‘আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলে, শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই; আমি সকল দেশের, সকল মানুষের।’ তাঁকে বিদ্রোহী কবির উপাধি দেওয়া হলেও এতে তাঁর খুব সায় ছিল বলে বোধ হয় না—
‘আমাকে বিদ্রোহী বলে খামখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতটাকে আঁচড়ে-কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনোদিনই নেই। আমি বিদ্রোহ করেছি, বিদ্রোহের গান গেয়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যা মিথ্যা-কলুষিত-পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে। ধর্মের নামে ভন্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কোনটাই নয়।’

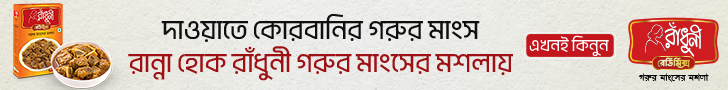
 Voice24 Admin
Voice24 Admin 





