নজরুল সম্পর্কে এ রকম কূটাভাসিক মন্তব্য সেকালে তো হয়েছেই, চলেছে আজও। ‘বর্তমানের কবি’—সেকালেই নজরুলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু সাময়িকতা নিংড়ে তাঁকে কবিতায় শব্দায়িত করে তোলার কাজ যে নজরুল করেছিলেন, তাঁর অকালনিস্তব্ধতার বছর ষাট পরে এ কথা দেদীপ্যমান হয়ে ফুটে আছে। শ্রেণির অভেদ কামনা করেছিলেন নজরুল, স্বাধীনতার আদীপ্র ঘোষণা দিয়েছেন তাঁর গদ্যে-পদ্যে-প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে; হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির গান গেয়েছেন। সাময়িকতার এই ব্যবহার নিয়েই হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচার কথা বলে (নজরুল তাঁর গদ্যেও রবীন্দ্রনাথের এই সংলাপ জানিয়েছেন আমাদের)। আমাদের এই ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যপ্রতিন্যাসের মধ্যে ছিল মৌলিক ব্যবধি। যা ছিল খবরের কাগজের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রবন্ধায়িত করেছেন। যেমন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে ঢের লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে করে তুলেছেন কবিতা। কবি জসীমউদ্দীন একবার একটি রচনায় নজরুলের কবিতাকে যে প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা দিয়েছিলেন, এ উক্তি সুপ্রযোজ্য। নজরুল ছন্দবদ্ধ প্রবন্ধই লিখেছেন অনেক কবিতায়, কিন্তু তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে কবিতার জিনিসপত্র প্রবেশ করিয়েছেন যে তা প্রাণবান হয়ে উঠেছে। ‘আমার কৈফিয়ত’ কবিতাটি প্রণীত হয়েছিল আশি বছর আগে, কিন্তু আজও যে তার গাত্রে শেওলা জমেনি, আজও যে কবিতাটি কাঁচা-তাজা জোশে টগবগ করছে, তার কারণ ওই প্রাণপূর্ণতা। হালকা চালে শুরু হয়েছে কবিতাটি, এগিয়েছেও হালকা চালেই, কিন্তু ক্রমেই মেঘ ঘনিয়েছে। ১৪টি স্তবকে সম্পূর্ণ হয়েছে কবিতাটি, ১৩টি স্তবক সমমাপ ও সুসমঞ্জস, নজরুলের প্রিয় ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে, বিস্ময়কর সব অন্ত্যমিলে নৃত্যপরায়ণ। শেষ ভিন্নধর্মী স্তবকে সব লঘুতার কুয়াশা ছিঁড়ে উচ্চারিত হলো একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও স্বপ্নময় প্রার্থনা:
‘পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথায় উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!’
শেক্সপিয়ারের সনেটের ১২ পঙ্ক্তির মেলবন্ধনের অন্তিমে শেষ দুই ছত্র যেমন হাতুড়ির আঘাতের মতো এসে পড়ে একটি অন্ত্যমিলের জোড়া, তেমনি এই মিলান্ত চতুষ্ক পুরো কবিতাটিকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে উন্মীলন/জাগরণ ঘটিয়েছে। অপরূপ, অদ্ভুত সেই জাগরণ। সেই জাগৃতিতে যেন পুরোনো কাব্যতত্ত্ব চুরমার হয়ে গেল। যুগসন্ধির কবি হিসেবে যশস্বী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তাঁর কালকে রূপায়িত করেছেন, কিন্তু তা পদ্যের স্তর অতিক্রম করতে পারেনি; নজরুলের কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি তাঁকে কবিতায় নিষিক্ত করেছেন।

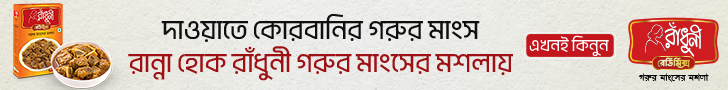
 Voice24 Admin
Voice24 Admin 





